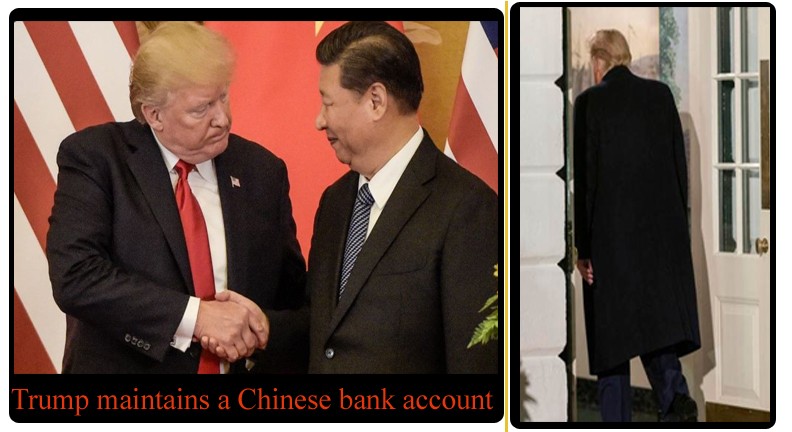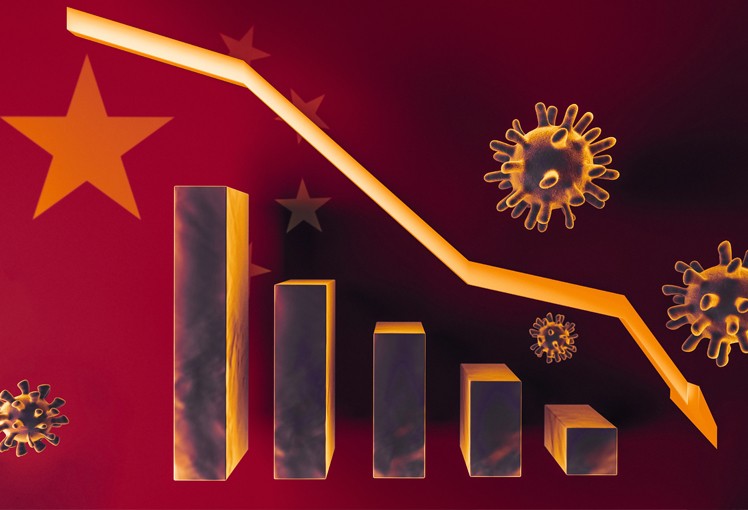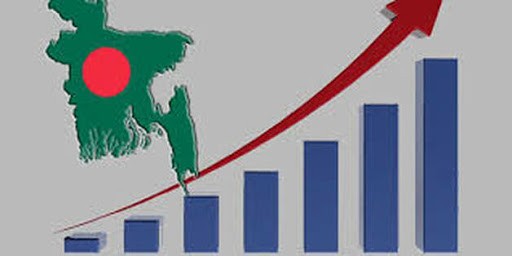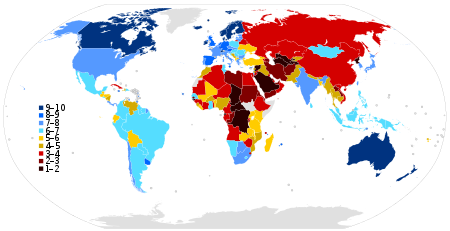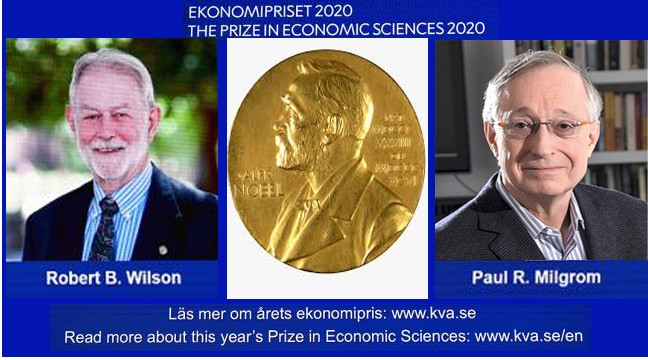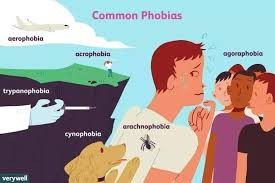ব্লুমবার্গে প্রকাশিত নিবন্ধ:ভারতকে প্রথমে বাংলাদেশকে পরাজিত করতে হবে
অ্যান্ডি মুখার্জী
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
লেখক ব্লুমবার্গ অপিনিয়ন বা মতামত বিষয়ক কলামনিস্ট। তিনি শিল্প ও আর্থিক খাত নিয়ে লেখালেখি করেন। এর আগে তিনি রয়টার্স ব্রেকিংনিউজের একজন কলামনিস্ট ছিলেন। এ ছাড়া তিনি কাজ করছেন স্ট্রেইটস টাইমস, ইটি নাউ এবং ব্লুমবার্গ নিউজে। এ লেখাটি ব্লুমবার্গে প্রকাশিত তার লেখা ‘দ্য নেক্সট চায়না? ইন্ডিয়া মাস্ট ফার্স্ট বিট বাংলাদেশ’ শীর্ষক লেখার অনুবাদ)
এ সপ্তাহে ভারতের কোভিড-১৯ অর্থনীতি অন্ধকার এক হতাশায় পরিণত
হয়েছে এমন এক খবরে, যেখানে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী বাংলাদেশের চেয়ে ২০২০ সালে মাথাপিছু
জাতীয় প্রবৃদ্ধি ভারতে কম হতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফ তাদের ওয়ার্ল্ড
ইকোনমিক আউটলুক আপডেট করার পর টুইট করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ
কৌশিক বসু। তাতে তিনি বলেছেন, যেকোনো উদীয়মান অর্থনীতি ভাল করছে এটা সুখবর। কিন্তু
এটা অবাক করে দেয়ার মতো খবর যে, ভারত এখন পিছিয়ে পড়ছে, পাঁচ বছর আগেও যারা অর্থনীতিতে
শতকরা ২৫ ভাগ সামনে ছিল।
১৯৯০ এর দশকে অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেয়ার পর থেকেই ভারতের স্বপ্ন হলো চীনের দ্রুত
বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা। এই প্রচেষ্টায় তিন দশকের চেষ্টার পর বাংলাদেশের
চেয়ে ভারত পিছিয়ে পড়ছে। এতে বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তিতে আঘাত লেগেছে। চীনের বিরুদ্ধে
অর্থপূর্ণ একটি পাল্টা অবস্থান প্রত্যাশা করে পশ্চিমারা।
কিন্তু সেই অংশীদারিত্বে এটা বলা হবে না যে, ভারত নিম্ন-মধ্যম
আয়ের ফাঁদে আটকা পড়বে।
তুলনামুলক নিম্ন দক্ষতা আত্মবিশ্বাসের ক্ষতি করতে পারে। যে ছোট্ট দেশটিকে ১৯৭১ সালে
স্বাধীন করতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ভারত, এখন ঘরের পিছনের সেই দেশটির
কাছে ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্খি ভারত পরাজিত হচ্ছে। এতে দক্ষিণ এশিয়ায় এবং ভারত মহাসাগরীয়
অঞ্চলে ভারতের প্রভাব ক্ষয় পেতে পারে।
ভুলটা কোথায় হয়েছে? অবশ্যই এ জন্য করোনা ভাইরাস মহামারী দায়ী। নতুন করে করোনা ভাইরাস
সংক্রমণ মধ্য জুনে বাংলাদেশে পিক-এ বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। অন্যদিকে ভারতে যেকোন
দেশের তুলনায় রেকর্ড উচ্চ হারে সংক্রমণের পর সবেমাত্র প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা কমে
আসতে শুরু করেছে।
বাংলাদেশে জনসংখ্যা সাড়ে ষোল কোটি। তার মধ্যে কোভিড-১৯ এ মারা গেছেন ৫৬০০ এর চেয়ে সামান্য
কম। অন্যদিকে এই জনসংখ্যার তুলনায় ভারতে রয়েছে আটগুন মানুষ। এখানে মৃতের সংখ্যা বাংলাদেশের
২০ গুন। আরো খারাপ বিষয় হলো, করোনা ভাইরাসের কারণে যে লকডাউন দেয়া হয়েছিল তাতে অর্থনীতির
মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। প্রকৃত আউটপুটের শতকরা ১০.৩ ভাগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে। এ তথ্য
আইএমএফের। বিশ্ব অর্থনীতি এতে যে পরিমাণ ক্ষতির শিকার হবে বলে মনে করা হচ্ছে, এই পরিমাণ
তার প্রায় আড়াই গুণ।
আর্থিক কৃপণতা, কম পুঁজির আর্থিক ব্যবস্থা এবং বহুবছরব্যাপী বিনিয়োগে পিছিয়ে আসায় ভারতের
করোনা পরবর্তী ক্ষতি মেটানো বিলম্বিত করবে। আরো খারাপ বিষয় হলো, করোনা বাদেও দৌড়ে বাংলাদেশের
কাছে হেরে যেতে পারে ভারত। এ বিষয়টি ‘ইন্ডিয়াস এক্সপোর্ট-লিড গ্রোথ: এক্সেম্পলার এন্ড
এক্সেপশন’ শীর্ষক একটি নতুন গবেষণাতে বর্ণনা করেছেন পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির
অর্থনীতিবিদ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতের সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ
সুব্রামানিয়ান। প্রথমেই ভারতের প্রবৃদ্ধির ব্যতিক্রমবাদের দিক বিবেচনা করা যাক।
বাংলাদেশ ভাল করছে। এর কারণ, তারা এর আগের এশিয়ান টাইগারদের পথ অনুসরণ করছে। তারা তাদের
কম দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি বজায় রেখেছে, যা গরিব দেশের কর্মবয়সী জনসংখ্যার সঙ্গে
সম্পর্কিত। এর চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছে ভিয়েতনাম। কিন্তু মৌলিকভাবে, উভয়েই চীনের কাছ
থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। কম দক্ষতাসম্পন্ন পণ্যের উৎপাদনের মাধ্যমে বড় আধিপত্য বিস্তার
করে, তার মাধ্যমে তারা উচ্চ জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে।
তবে ভারত অন্য পথ অবলম্বন করেছে। সেখানে ১০০ কোটি মানুষের কারখানায় কর্ম উপযোগী বা
কর্মবয়সীদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তারা সেই পথ বেছে নেয়নি। ওই দুই লেখক লিখেছেন,
ভারতে কম দক্ষতাসম্পন্ন বস্ত্রশিল্পে এবং পোশাক খাতে যে পরিমাণ উৎপাদন মিসিং হয়েছে
বা হারিয়েছে, তার পরিমাণ ১৪০০০ কোটি ডলার, যা ভারতের জিডিপির শতকরা প্রায় ৫ ভাগ।
ভারতের কমপিউটার সফটওয়্যার প্রযুক্তির অর্ধেকও যদি ২০১৯ সালে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যেতো,
তাহলে হইচই পড়ে যেতো। কিন্তু ওই ৬০০ কোটি ডলার হারানো আর বার্ষিক কম দক্ষতাসম্পন্ন
উৎপাদন রপ্তানি একই। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু এ নিয়ে কেউই কোনো কথা বলতে চান না। নীতিনির্ধারকরা
মানতে চান না যে, জুতা এবং বস্ত্র কারখানা, যা জোর করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তা থেকে
ডলার আয় হতে পারতো এবং কর্মসংস্থান হতো বিপুল সংখ্যক মানুষের। এর ফলে গ্রাম থেকে শহরমুখী
অভিবাসীদের কাছে স্থায়ী কর্মসংস্থানের একটি পথ তৈরি হয়ে যেতো।
যেসব কর্মক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা এমনটা করতে পারেনা কখনোই।
বাংলাদেশে কর্মবয়সী নারীদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে দু’জন শ্রমে যুক্ত। ভারতে এক্ষেত্রে
অংশগ্রহণের শতকরা হার ২১ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশে এই হার ভারতের দ্বিগুন।
আরো বিপদের বিষয় হলো, সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে, রাজনীতিকরা তাদের অতীতের
ভুলকে দ্বিগুন করতে পারেন এবং তাদের স্বয়ম্ভরতায় মুক্তি খুঁজতে পারেন: ‘বাংলাদেশের
চেয়েও গরিব? কিছু মনে করবেন না। আমরা আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারি এবং আমাদের
আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারি। এমন করেই আমাদেরকে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে
দিন’। আকস্মিকভাবে ১৯৬০ এর দশক ও ১৯৭০ এর দশকের আত্মনির্ভরশীলতার স্লোগান ভারতের অর্থনৈতিক
নীতিতে ফিরেছে।
এই হতাশাকে দূর করতেই আবার সামনে আসে চট্টপাধ্যায় ও সুব্রামানিয়ানের গবেষণা: ‘জনবিশ্বাসের
বিপরীতে, ভারত রপ্তানিনির্ভর প্রবৃদ্ধিতে একটি অনুকরণীয় অবস্থানে রয়েছে। চীন ও ভিয়েতনাম
বাদে সব দেশের চেয়ে ভাল করছে ভারত। আসলে মূল কথার অর্ধেকের সামান্য পূর্ণ।
দেশের জন্য কাজ হয়েছে বাণিজ্যে। এটি একটি মারাত্মক ভুল। কারণ, দুই গবেষক দেখিয়েছেন-
‘বিশেষত্বকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তুলনামুলক সুবিধার বিষয়টি অস্বাভাবিক পর্যায়ে
রয়েছে’। উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্য ও সেবার প্রচুর রপ্তানি করে ভারত।
যেমন কম্পিউটার সফটওয়্যার। কিন্তু বিশ্বের কারখানা হিসেবে পরিচিত চীন এখন নিচে থাকা
অন্যদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছে। শুধু স্বাস্থ্যখাতে অথবা সুশিক্ষিত শ্রমের ওপর নয়, তুলনামুলক
সস্তার সুবিধা তারা নিচ্ছে, সেখানেই ভারতের সুযোগগুলো রয়েছে বাস্তবে।
বছরে পর বছর কমপক্ষে ৮০ লাখ কর্মসংস্থানের জরুরি চ্যালেঞ্জের মুখে এটাই হলো ভারতের
করোনা পরবর্তী সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা।